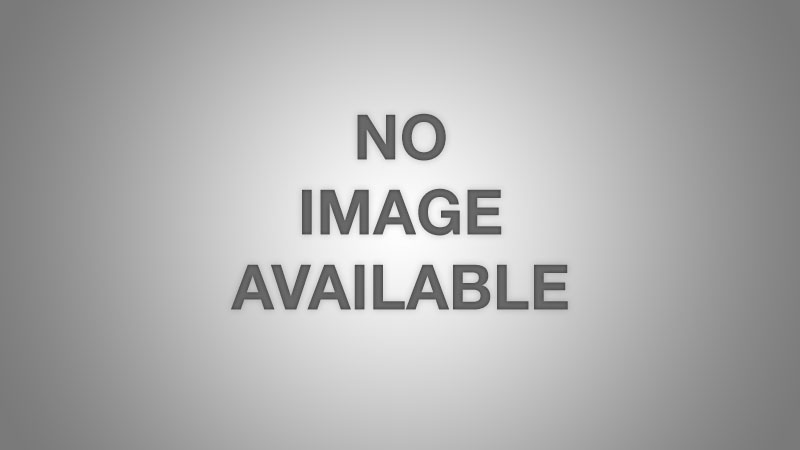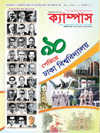৮০তম জন্মদিনেও অবিচল এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ -এই সাহসী আর গর্বের লড়াইয়ে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। রাজনৈতিক কর্মী হয়ে লিখেছেন ভাষা আন্দোলনের ইশতেহার, শিক্ষক হিসেবে দেখিয়েছেন স্বাধিকার আন্দোলনের উজ্জ্বল পথ। আবার ২৩ বছরের পাকিস্তানি অপশাসন শেষে রচিত হয় যে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান, সেখানেও তাঁর স্পর্শ। তিনি জাতির বাতিঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।
সম্প্রতি বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে ফেরার নয় দিনের মাথায় পিঠে ব্যথা নিয়ে আবার হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন।
তবে জন্মদিন বলে চিকিৎসকদের বলে এই অধ্যাপককে সাময়িক সময়ের জন্য বাসায় নিয়ে গেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই এমিরেটাস অধ্যাপকের ৮০ তম জন্মবার্ষিকী ঘিরে নানা আয়োজন রয়েছে।
ঠান্ডাজনিত অসুস্থতার সঙ্গে মেরুদন্ডে তীব্র ব্যথা অনুভবের পর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে থাইল্যান্ড নেয়া হয়েছিল অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে। চিকিৎসা নিয়ে তিনি গত ৯ ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরেন।
এই ক’দিন কিছুটা ভালো থাকলেও পিঠের ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় আবার তাকে বিএসএমএমইউতে নেওয়া হয়। তার ছেলে আনন্দ জামান বলেন, থাইল্যান্ডের চিকিৎসক বলেছিলেন, পিঠে ব্যথা সেরে যাবে। কিন্তু কোনো উন্নতি হয়নি। যেহেতু তার ৮১তম জন্মদিন, তাই তাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনা হয়েছে। বাবার ছাত্র, অনুরাগীরা তাকে দেখতে আসছেন, বলেন আনন্দ।
৮০তম জন্মদিন তাঁর। ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মেছিলেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটে। যৌবনের শুরুতেই বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গী- ১৯৫২। আনিসুজ্জামানের বয়স সবে ১৫। তখনই তাঁর ওপর দায়িত্ব বর্তাল পাকিস্তান যুবলীগের দপ্তর সম্পাদকের। যুবলীগের পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে একটি পুস্তিকা বের করার সিদ্ধান্ত হয়। আর দায়িত্ব নিয়ে কিশোর আনিসুজ্জামান বের করে ফেলেন ভাষা আন্দোলন কী, কেন? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একদিন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ বললেন, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ থেকে তোয়াহা সাহেবকে একটা পুস্তিকা লেখার ভার দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি সময় পাচ্ছেন না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতার বিষয়ে আপনি একটি পুস্তিকা লিখে ফেলেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তার পরও পুস্তিকাটি লিখলাম। অলি আহাদ সংশোধন করে দিলেন। এতে কারো নাম ছিল না।
২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালানোর পরের দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে দেয়া বক্তব্যে আনিসুজ্জামান দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, শাসকশ্রেণির ভাড়া খেটে পুলিশের কোনো লাভ নেই।
স্বৈরাচার আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে
পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন চলছে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জয়ন্তী চলে এলো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র চর্চা তখন প্রায় নিষিদ্ধ। আনিসুজ্জামানের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দিনটি পালন করলেন। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেন, ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী বললেন, পাকিস্তানের ভাবাদর্শের পরিপন্থী বিধায় সরকারি প্রচারযন্ত্র থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার কমানো হয়েছে। সেদিনই আমরা এর প্রতিবাদ করলাম। ১৯ জন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর এক দিনের মধ্যে আমি জোগাড় করলাম। বিবৃতি দেওয়া হলো। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা হয়ে উঠলেন।
মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক
একাত্তরের ২৫/২৬ মার্চ ভয়াবহ গণহত্যা চালানোর পর ৩১ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মস্থল থেকে তিনি ভারতে চলে যান। কলকাতায় গঠন করেন বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতি। ড. এ আর মল্লিক হলেন এর সভাপতি, আর আনিসুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক। বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন তিনি। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। আনিসুজ্জামান যোগ দেন তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকারের ‘পরিকল্পনা সেলে’। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রেহমান সোবহানের পরামর্শে তত দিনে তাজউদ্দীন সাহেব ঠিক করেছেন, একটি পরিকল্পনা সেল গঠন করবেন। প্রথমে খান সারওয়ার মুরশিদ, মোশাররফ হোসেন, স্বদেশ বসু ও আমাকে নিয়ে একটি কমিটি করা হলো। পরে ড. মুজাফফর আহমদকে চেয়ারম্যান করে সেলটিকে পরিকল্পনা কমিশন করা হয়। এর মধ্যে সারওয়ার মুরশিদ ও আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে বক্তৃতা লেখার কাজে সাহায্য করতাম। তিনি নিজে খুব ভালো ইংরেজি ও বাংলা জানতেন। তাঁর পরও চাইতেন, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে থাকি।
স্বাধীনতার পর সংবিধান রচিত হয় ইংরেজিতে। এর বাংলা তর্জমার দায়িত্ব পান আনিসুজ্জামান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার। আমাদের সংবিধানের খসড়াটি ইংরেজিতে তৈরি করা হয়েছিল, সেটির বাংলা ভাষ্য তৈরির দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হলো। স্কুলজীবনের সহপাঠী নেয়ামুল বসিরকে সঙ্গে নিলাম। সে গণপরিষদের বিতর্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিল। ওই অফিসের আরেকজনকে নিয়ে আমরা কাজ শুরু করলাম। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে কাজ শুরু করে নভেম্বরে শেষ করলাম। পরে এটি পরীক্ষার জন্য সৈয়দ আলী আহসান, মজহারুল ইসলাম ও আমাকে নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক কমিটি করা হয়। গণপরিষদের রেকর্ডে আমাদের তিনজনের নাম আছে।
তাঁর কৃতী ছাত্ররা ছড়িয়ে আছেন দেশজুড়ে
দেশের বহু কৃতী ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক ও কবির শিক্ষক আনিসুজ্জামান। এ কারণে অনেকে তাঁকে শিক্ষকদের শিক্ষক বলেন। প্রয়াত কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, হায়াৎ মাহমুদ, মনজুরে মওলা, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, মনসুর মুসা, হুমায়ুন আজাদ, সৈয়দ আকরম হোসেন, আবুল কাশেম ফজলুল হক, আহমদ কবির, হুমায়ুন কবীরের মতো গুণীজনরা ছিলেন আনিসুজ্জামানের ছাত্র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গর্বভরে বলেন, তিনি আনিসুজ্জামানের ছাত্রী। শিক্ষক হিসেবে নিজের অবস্থান বিষয়ে আনিসুজ্জামান বলেন, আমার একটি খুশি হওয়ার ব্যাপার আছে যে নানা জায়গায়, নানা ক্ষেত্রে আমার ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষকতা করে আমি তৃপ্তি পেয়েছি।
পরিবার থেকে পেয়েছিলেন উৎসাহ
আনিসুজ্জামানের বাবা এ টি এম মোয়াজ্জেম ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। মা সৈয়দা খাতুন গৃহিণী হলেও লেখালেখি করতেন। পিতামহ শেখ আবদুর রহিম ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে আনিসুজ্জামান চার নম্বর। পরিবার থেকেই অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন।
দেশের প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছিল। কোনো এক মা শহীদ মিনার দেখতে এসে একটি সোনার হার দিয়ে গিয়েছিলেন। হারটি বহুদিন মেডিকেল কলেজে রাখা হয়েছিল। সেটি দিয়েছিলেন আনিসুজ্জামানের মা আর হারটি ছিল আনিসুজ্জামানের মৃত বোনের।
সেদিনের স্মৃতি মনে করে আনিসুজ্জামান বলেন, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানোর পর ২২ ফেব্রুয়ারিই প্রথম শহীদ মিনার গড়ে উঠল। সেখানে অনেকে গিয়ে টাকা-পয়সা দিয়েছেন। তখন আমি জানতাম না যে মা আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে আমার মৃত ছোট বোনের সোনার হার শহীদ মিনারে দিয়ে এসেছিলেন। এই ঘটনা নিয়ে মুর্তজা বশীরের একটি কবিতাও আছে। বশীরও তখন জানত না যে সেটি আমার মা দিয়েছেন। তখন এটি বেশ আলোড়ন তুলেছিল। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ছিলাম। পুলিশ এসে মিনারটি শাবল দিয়ে ভেঙে ফেলে।
স্বমহিমায় উজ্জ্বল আনিসুজ্জামান
আনিসুজ্জামান বাংলার শিক্ষক হয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। কর্মজীবন শুরু করেন মাত্র ২২ বছরে। ‘ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)’ বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি বৃত্তি নিয়ে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান।
আনিসুজ্জামান বিভিন্ন সময় লন্ডন ও জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ (কলকাতা), প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। আনিসুজ্জামান বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।
আনিসুজ্জামানের ত্রিশের বেশি গবেষণাগ্রন্থ রয়েছে। এ ছাড়া অনুবাদ, সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরোর ওপরে। উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, মুনীর চৌধুরী, স্বরূপের সন্ধানে, মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর ইত্যাদি। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রবীন্দ্রনাথ।
আনিসুজ্জামান বিভিন্ন সময় দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন। এসবের মধ্যে আছে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার। ভারত সরকারও তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাপূর্ণ পদ্মভূষণ পদকে ভূষিত করে ২০১৪ সালে।
লেখালেখি ও শিক্ষকতায় এখনো সক্রিয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইমেরিটাস অধ্যাপকের মর্যাদা দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে তাঁর শারীরিক অবস্থা তেমন ভালো যাচ্ছে না। ঠান্ডাজনিত নানা উপসর্গের সঙ্গে মেরুদন্ডে ব্যথার কারণে চিকিৎসার জন্য তাঁকে ব্যাংককে নিয়ে যাওয়া হয়। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরার পর থেকে তিনি বিশ্রামে রয়েছেন। এ কারণে তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানমালা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আনিসুজ্জামানের জন্মদিন উদ্যাপন ও তাঁর জীবন-কর্মভিত্তিক তথ্যচিত্র ‘বাতিঘর’-এর প্রিমিয়ার শো উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।